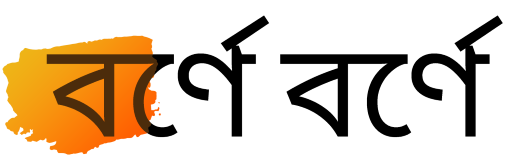রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর আধুনিকতা
অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়,
নয়ডা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। মোগল সাম্রাজ্য তখন অস্তাচলে। ভারতবর্ষ বলে
কোনও দেশের অস্তিত্ব তখন ছিল না। খণ্ড খণ্ড হয়ে রাজারা তখন জমির দখল নিয়ে
লড়ে চলেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও আজকের দিনে ‘দেশাত্মবোধ’ বলতে আমরা যা
বুঝি, গড়ে ওঠেনি তেমন চেতনা। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে তাদের
মুঠি ক্রমশ শক্ত করে চলেছে বাণিজ্যিক স্বার্থে। বাংলা তথা ভারতের অন্য
জায়গাতে মানুষ জাতপাত আর কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবে আছে। এমন সামাজিক
পটভূমিকায় বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে ইউরোপের নবজাগরণের ঢেউ এসে লাগল, যার
অন্যতম পথিকৃৎ হয়ে উঠলেন কোলকাতায় রামমোহন রায়।
খুব অল্প বয়স থেকেই মেধাবী রামমোহন বিভিন্ন ধর্মের দার্শনিক দিক নিয়ে
চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। রামমোহনের বাবা তাঁকে বেনারস পাঠান হিন্দুধর্ম
চর্চা করার জন্য। এরপর রংপুরে তিনি তন্ত্রবিদ্যার তালিম নেন। বৌদ্ধ
ধর্মের পাঠ নিতে চলে যান তিব্বতে। সেখানেই তাঁর জ্ঞানের অনুসন্ধান থেমে
থাকে না। তিনি ইসলাম ধর্মের উপর পড়াশুনো করার জন্য যান পাটনায়। ফার্সি ও
আরবি ভাষাও শিখে নেন। কোলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পাঠ নেন খৃষ্টধর্মের।
নানা ধর্মের ভাবধারার সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। সূফী ধারার উপর প্রচুর
পড়াশুনো করেন রামমোহন। তাই তাঁকে এই দেশের প্রথম চিন্তাশীল তুলনামূলক
ধর্মতত্ত্বের প্রবক্তা বলা যায়।
কোলকাতায় স্থাপিত এশিয়াটিক সোসাইটির সংস্পর্শে এসে রামমোহন হিন্দু ধর্মের
পৌত্তলিকতাকে সোজাসুজি চ্যালেঞ্জ করে বসেন। এর ফলে তাঁকে তদানীন্তন
ব্রাহ্মণ সমাজের প্রচুর গালমন্দের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু দৃঢ়চেতা পুরুষ
রামমোহন ধর্মগুরুদের শাসন-ত্রাসনকে খুব সহজেই তুচ্ছ করে দিতে পেরেছিলেন।
সতীদাহর মত ঘৃণ্য প্রথার বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার হয়ে ওঠেন।
সমাজের কুপ্রথার বিরোধিতার সপক্ষে রামমোহন যুক্তি দিয়ে বলেন যে, তিনি
ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিপক্ষে কখনই নন, কিন্তু ধর্মীয় কুপ্রথা ও আচারের
বিরোধিতা করছেন মাত্র। জাতপাতের কারণেই যে ভারতবাসী বিভক্ত এবং বিদেশীদের
বিরুদ্ধে একজোট হয়ে নিজেদের দেশ গড়ে তুলতে অক্ষম, সেই কথা তিনি সোচ্চারে
বলতে থাকেন। রামমোহনের চিন্তাজগতে যুক্তিবাদ ধর্মীয় অনুশাসনের চাইতে অনেক
ঊর্ধে স্থাপিত হয়। তাঁর এই মননশীলতা প্রভাব ফেলে বহু ভারতীয় চিন্তাবিদের
মধ্যে। এমনকি এদেশে চাকুরীজীবী হয়ে আসা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনেক
রাজপুরুষও রামমোহনের সমর্থক হয়ে পড়ে।
তখন সমাজে এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের কোনও পুস্তক পড়লে তাকে বিধর্মী
বলে দাগ দিয়ে দেওয়া হত এবং সমাজে বাস করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে
যেত। রামমোহন স্কুলের ছাত্রদের বলতেন, সব ধর্মপুস্তক পড়লে তবেই প্রকৃত
দর্শন জানা সম্ভব। তিনি নিজের উদাহরণ দেখিয়ে বলতেন, যেমন তিনি সব ধর্মের
পুস্তক পড়া সত্ত্বেও আগাগোড়া হিন্দু হয়ে রয়েছেন, তেমনই তারা যদি অন্য
ধর্মের বই পড়ে, তবে জাত যাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না।
ইউরোপীয় চিন্তাবিদ ফ্রন্সিস বেকনের শিক্ষা রামমোহনকে সবচাইতে বেশি
প্রভাবিত করে। বেকনের মতে মনুষ্যসমাজের উন্নতির জোয়ার এনে দিয়েছিল
বিজ্ঞানের অগ্রগতি। বারুদ, কম্পাস এবং ছাপাখানার আবিষ্কার মানবসভ্যতাকে
অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যায়। কম্পাস দিয়ে ইউরোপীয়রা অভিযান চালিয়ে
নানা দেশে গিয়ে বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়েছে। আর এই কাজে
তাদের সহযোগিতা করেছে কম্পাস, যা দিয়ে তারা সঠিকভাবে তারা দিক নির্ণয়
করতে পেরেছে। বারুদ ব্যবহার করে নিজেদের সুরক্ষিত রেখে তারা চালিয়ে গেছে
অভিযান, যার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে পৃথিবীর নতুন নতুন ভূখণ্ড, জানা গিয়েছে
অজানা প্রকৃতির নানা রহস্য।
প্রখর যুক্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রামমোহনের সামাজিক–সাংস্কৃতিক চিন্তার
বৈপ্লবিক দর্শন জানা যায় রামমোহনের বিভিন্ন লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে।
ইংল্যান্ডের দার্শনিক জন লোকে-র দর্শন রামমোহনের সামাজিক চেতনায় বিপ্লব
আনে। লোকে ছিলেন বেকনের বৈজ্ঞানিক ভাবনায় দীক্ষিত। তাঁর ভাবশিষ্য রামমোহন
মনে করতেন —পুরোহিত শ্রেণীই হোক কী রাজা, কারো সম্পূর্ণ অধিকার নেই
প্রজাদের স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ করার। প্রজা যেহেতু রাজা বা পুরোহিতকে
নির্বাচিত করে, তাই তাদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব একমাত্র
শাসকের উপর বর্তায়। তবে প্রজাদের মৌলিক অধিকারের কিছু কিছু অংশ ত্যাগ
করতে হয় সামাজিক বিকাশের স্বার্থে। যদি প্রজাদের বৃহত্তর স্বার্থ ব্যহত
হয়, তবে তাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে শাসক শ্রেণীকে উচ্ছেদ করার। সপ্তদশ
শতকে এই চিন্তাভাবনা ছিল যথেষ্ট বৈপ্লবিক এবং কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে
ডুবে থাকা ভারতে রামমোহনের ভাবনা সমাজবদলের দিশা দেখায়।
রামমোহন মনে করতেন, মানুষের চিন্তাজগতে বিপ্লব ঘটার রাস্তা হল বিজ্ঞান
চেতনা। ইউরোপীয় সমাজ-জাগরণ এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ। কাজেই যুক্তিবাদী মন
নিয়ে রামমোহন এই দেশে বিজ্ঞান বিকাশের প্রয়োজনের কথা প্রচার করতে শুরু
করেন। প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ তখন জীর্ণ ও পুরাতন। ইউরোপ বহু
আগে এগিয়ে গিয়েছে বিজ্ঞান গবেষণায়। নিউটন ততদিনে মহাকর্ষের সূত্র লিখে
ফেলেছেন। সুপণ্ডিত রামমোহনের কাছেও সেই সব আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার
সংবাদ অবিদিত ছিল না।
প্রথম প্রথম রামমোহনের বক্তৃতা ও লেখায় ব্রিটিশ বিদ্বেষের কথা শোনা গেলেও
পরবর্তীকালে তিনি এই দেশে বিজ্ঞানের বিকাশের জন্য ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে
আসার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করতে থাকেন। ১৮২৮ সালে জেমস ক্রফোরড-কে
লেখা এক চিঠিতে তিনি লিখছেন, “যদি ইউরোপীয়দের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করে
এবং আধুনিক শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে এদেশীয় মানুষেরা ১০০ বছর
পর সামাজিক ও মানসিক দিক থেকে উন্নত হয়ে যায়, তবে তখন কি আর তাদের
বিরুদ্ধে ঘটতে থাকা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে না?”
তাই গণজাগরণে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা রামমোহন সকলের সামনে তুলে ধরেন।
সেই সময়ে কোলকাতায় সংস্কৃত কলেজ গড়ে তোলার পরিকল্পনা হচ্ছিল। রামমোহন এই
কলেজে শুধু সংস্কৃত ভাষা চর্চার বিরোধিতা করতে থাকেন। তিনি লন্ডনে
ব্রিটিশ সরকারের কাছে চিঠি লিখে জানান— ভারতের মাটিতে সংস্কৃত কলেজের
বদলে ইউরোপীয় শিক্ষার ধাঁচে বিজ্ঞান বিষয় পড়ানোর জন্য কলেজ স্থাপন করা
আরও বেশি প্রয়োজন।
১৮২৩ সালে লর্ড আরমহারস্টকে রামমোহন এক চিঠিতে লিখছেন – “...মহামান্য
ইংল্যান্ড সরকার ভারতে দেশীয় মানুষদের শিক্ষা দেবার জন্য আর্থিক সহায়তার
দিচ্ছেন, যা আমার জানা আছে। আমরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি যে সেই অর্থের
একটি অংশ অন্তত ইউরোপীয় উচ্চশিক্ষা, যে শিক্ষা তাদের অন্যান্য দেশের
চাইতে অনেক উঁচুতে স্থান দিয়েছে, সেই শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষকদের দ্বারা
করাটাই বাঞ্ছনীয়। ভারতীয় ছাত্রদের অঙ্ক, প্রাকৃতিক দর্শন, রসায়ন,
শল্যচিকিৎসা, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দেবার কাজ
খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
...আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সংস্কৃত কলেজ স্থাপনে সরকারি উদ্যোগের ফলে
শুধুমাত্র হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা এই দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির উপরই শুধু
শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। সেই শিক্ষা আগামী প্রজন্মকে কেবলমাত্র ব্যাকরণ ধর্মী
শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে, সামাজিক উন্নতির কোনও সম্ভাবনা তাতে নেই।”
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞান চিন্তক অক্ষয় কুমার দত্ত রামমোহনের উপরোক্ত
মতবাদের জন্য তাকে স্মরণ করেছেন বারবার। ভারতের নব জাগরণের উন্মেষের
অন্যতম পথিক বলে রামমোহনকে ভূষিত করেন তিনি।
উইলিয়াম কেরি ১৭৯৩ সালে কোলকাতায় আসেন খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য। ইস্ট
ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধিতায় (তারা নন ব্যাপটিস্ট ছিল) কেরি কোলকাতার
পার্শ্ববর্তী শহর শ্রীরামপুরে এসে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে স্থাপনা করেন
শ্রীরামপুর মিশনারি। এই মিশনারি থেকে খৃষ্টধর্ম প্রচার ছাড়াও চাষবাস,
উদ্ভিদবিদ্যা এবং জীবন বিজ্ঞানের পাঠ দেওয়া হত। রামমোহন কেরির খুব ঘনিষ্ঠ
বন্ধু ছিলেন। এই মিশনেই তাঁর পরিচয় হয় ডেভিড হেয়ারের সাথে। ১৮২০ সালে
কেরি ‘এগ্রি- হর্টি কালচার সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া’ স্থাপন করেন। তার তৈরি
বাগানে প্রায় ৪২৭টি দুর্লভ প্রজাতির গাছ লাগানো হয়। কোম্পানির অধীনে
শিবপুরে যে বটানিকাল গার্ডেন ছিল, তার চাইতেও বেশি নাম করে কেরির বাগান।
এখানে ভারতের উদ্ভিদের উপর গবেষণার কাজ শুরু করান উইলিয়াম কেরি। এই
সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ভারতে উন্নতমানের চাষআবাদ নিয়েও নানা পরীক্ষা
নিরিক্ষা চলতে থাকে। কেরির নেতৃত্বে শ্রীরামপুর মিশন বৈজ্ঞানিক
চিন্তাভাবনার উন্মেষে অনেক দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে থাকে।
উইলিয়াম কেরির চেষ্টায় শ্রীরামপুর মিশনে ছাপাখানা বসানো হয়। ভারতে বই
ছাপা হওয়া তখন সবে শুরু হয়েছে। ব্রিটিশরা ছাপাখানা আমদানি করে ভারতের
নানা জায়গায় বসালেও তাদের উপনিবেশিক স্বার্থেই সেই ছাপাখানাগুলো ব্যবহার
করা হত। কিন্তু কেরির ছাপাখানা থেকে প্রথম বাংলা বই ছাপা হয়— রামরাম বসুর
লেখা প্রতাপাদিত্য চরিত্র।
কেরির ছাপার কাজে তার সহায়ক পাদ্রি উইলিয়াম ওয়ার্ডের অবদান অসামান্য।
তিনি ছিলেন কাগজ ছাপানোর একজন ওস্তাদ কারিগর। শ্রীরামপুর মিশনারিতে একজন
ভারতীয়কে উইলিয়াম কেরি কাজ দেন। তিনি হলেন পঞ্চানন কর্মকার। জাতে লৌহকার
ছিলেন পঞ্চানন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে বাংলা হরফ কাটার ইউরোপীয় কায়দা
রপ্ত করে ফেলেছিলেন। মিশনে পঞ্চানন কর্মকার যোগ দেওয়ায় কাজ চলতে থাকে
দ্রুত। তিনি মিশনের ছাপাখানার ধাতু ঢালাই করে অক্ষর তৈরি করার প্রশিক্ষণ
দিতেন নতুন কাজে যোগ দেওয়া স্থানীয় তরুণদের। শ্রীরামপুরের ছাপাখানার সাথে
পঞ্চানন কর্মকারের নাম জড়িয়ে ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে।
ছাপাখানার অগ্রগতির সাথে সাথে প্রয়োজন হল প্রচুর কাগজের। কাগজ বানানোর
কারখানা খোলা হল শ্রীরামপুরে। প্রথম প্রথম মানুষের পেশি শক্তিতে চলত কাগজ
বানানোর কল। তখন ইংল্যান্ডে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার হয়ে গেছে। কেরি
শ্রীরামপুরে ছোট বাষ্পচালিত কাগজের কল খুলে ফেললেন। ইস্ট ইন্ডিয়া
কোম্পানি কেরিকে জব্দ করার জন্য রানিগঞ্জের কয়লার উপর চড়া মাশুল বসিয়ে
দিল। কেরি তাতেও পিছপা নন। এবার তিনি টিটাগড়ে কাগজ বানানোর কারখানা খুলে
ফেলে ছোট বাষ্পচালিত ইঞ্জিন বানাবার দায়িত্ব দিলেন গোকুল চন্দ্র নামের এক
ওস্তাদ কারিগরকে। শ্রীরামপুর মিশনের ধাঁচে গোকুল ইঞ্জিন বানিয়ে তাক
লাগিয়ে দিলেন। এটিই ভারতের প্রথম স্বদেশি যন্ত্র, যার কারিগরও ছিলেন একজন
ভারতীয়। এই যন্ত্রটি জনসমক্ষে দেখানো হয় কোলকাতার টাউন হলে। স্বভাবতই
জনপ্রিয়তা ও কার্জ দক্ষতার কারণে শ্রীরামপুর ও টিটাগ্রে তৈরি কাগজ
ব্রিটিশদের বানানো কাগজের চাইতে সস্তা হয়।
কোল ব্রুকের চেষ্টায় ১৮০৬ সালে উইলিয়াম কেরি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পড়ানোর
জন্য ডাক পান এবং এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে সদস্য করে নেয়। এশিয়াটিক
সোসাইটি স্থির করে এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় দর্শন, জীববিজ্ঞান,
চিকিৎসাশাস্ত্র ও শিল্পকলা যোগ করা হবে। কেরি জীববিজ্ঞানের পাঠ দেওয়ায়
অগ্রণী ভুমিকা নেন। তিনি মাত্রিভাশায় বিজ্ঞান শেখার উপর সবচাইতে বেশি
গুরুত্ব দেন।
এশিয়াটিক সোসাইটি ও অন্যান্য চিন্তাবিদের চাপে পড়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি
এক চার্টার জারি করে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য বার্ষিক এক
লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে, যাতে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়।
কেরির জনপ্রিয়তা কোম্পানির প্রটেস্টান্ট বিরোধী মনোভাবের বদল ঘটায়।
এই চার্টার জারি করার পর কাজের কাজ কিছুই হয় না। লর্ড মিন্টো ফোর্ট
উইলিয়াম কলেজে এসে সংস্কৃত, ফার্সি এবং আরবি ভাষায় লুকিয়ে থাকা বিজ্ঞানের
খোঁজ করতে নির্দেশ দেন। কেরি আবার মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও ইউরোপীয়
বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দিয়ে একটি পত্র লেখেন মিন্টোকে। তিনি নিজে অঙ্ক
ও বিজ্ঞান শেখাবেন, সে কথাও উল্লেখ করেন। শ্রীরামপুর মিশনের পথে হেঁটেই
যে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব, সে কথাও তিনি জোরের সাথে প্রচার করতে
থাকেন। কেরির সেই পত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাঠক্রমের আওতায় আনার কথা
জোরের সাথে বলা হয়।
১) সৌরমণ্ডল
২) গতিসূত্র ও মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব
৩) সাধারণ দর্শন- আলো, তাপ, বাতাস, জল, বায়ুমণ্ডল, রসায়ন, খনিজবিদ্যা ও
ইতিহাস
৪) ভূগোল, বারুদের আবিষ্কার ও ব্যবহার, ছাপার কারিগরি, কম্পাসের ব্যবহার,
ভারত-চিন সম্বন্ধীয় তথ্য
৫) শরীর, মন, নীতিশাস্ত্র, নৈতিকতা
১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপনা হয় কেরির প্রচেষ্টায়। এই কলেজে
ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়। রামমোহন ও অনেক
শিক্ষাবিদ কেরির স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে আসেন। মিশনের কাজে
রামমোহন যোগ দেওয়ার সাথে সাথে কোলকাতায় ব্রাহ্মণরা তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার
হয়ে ওঠে। রামমোহনের বিরুদ্ধে চক্রান্তও শুরু হয়ে যায়।
১৮১৭ সালে একটি যুগান্তকারী সংস্থা খোলা হয় কেরির চেষ্টায়। ক্যালকাটা
স্কুল বুক সোসাইটি। এই সংস্থার মাধ্যমে স্কুল-পাঠ্য বইয়ের আমূল সংশোধন
করে প্রচুর বই ছাপার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তদানীন্তন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদেরা
এই কাজে সাহাজ্যের হাত বাড়িয়ে দেন। লর্ড হেস্টিংস ব্যক্তিগত ভাবে উৎসাহ
নিলে কাজের পালে ঢেউ লাগে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার , রাম কমল সেন,
রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, এবং রামমোহন রায়ের মত বিশিষ্ট মানুষের
চেষ্টায় শিক্ষাজগতের উন্নতি হতে থাকে।
জন ক্লার্ক মারস্ম্যান এই একই সময়ে শ্রীরামপুর মিশনে যোগ দেন। তিনি এই
দেশের মাটিতে জন্মান ও ছেলেবেলা থেকেই বাংলাভাষায় খুব দ্রত পারদর্শিতা
লাভ করেন। দিগদর্শন, সমাচার দর্পণ ইত্যাদি পত্রপত্রিকা তাঁর হাতে
সম্পাদিত হতে থাকে। তাঁর লেখা বই জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায় খুব জনপ্রিয়তা লাভ
করে। একই সময়ে উইলিয়াম হপকিন্স স্পিয়ার্সের লেখা বই ভূগোল বৃত্তান্ত
প্রকাশিত হয় স্কুল বুক সোসাইটি থেকে। এরপর তিনি পশ্বাবলী নামে পশুপাখিদের
উপর একটি বই লেখেন স্কুল পড়ুয়াদের জন্য।
আর এক ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ উইলিয়াম ইয়েটস্ পদারথবিদ্যার
শিক্ষার জন্য পদার্থবিদ্যাসার লেখেন। প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্পর্কীয় নানা
আধুনিক তথ্য এই বইটিতে পাওয়া যায়।
উইলিয়াম কেরির পুত্র ফেলিক্স কেরিও বাবার মত বাংলা ভাষার পণ্ডিত হয়ে
ওঠেন। শিক্ষা শেষ হবার পর তিনি এন্সলাইকপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে অনুবাদ
করে ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা নামে একটি বই প্রকাশ করেন। দুই খণ্ডে প্রকাশিত এই
বইটিতে মানবদেহের হাড়ের গঠন ও অন্যান্য অঙ্গের কার্যকারিতা সম্পর্কে
প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়।
এই অসামান্য মিশনের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে চলতে রাজা রামমোহন রায়
একটি বই লেখেন যাতে জ্যামিতি ও ভূগোলের প্রচুর আলোচনা করেন। ‘জ্যামিতি’ ও
খগোল’ দুটি শব্দের জনকও তিনি।
উইলিয়াম কেরির চেষ্টায় একজন অত্যন্ত গুণী বিজ্ঞান শিক্ষক শ্রীরামপুর
মিশনে যোগ দেন, তিনি হলেন- জন ম্যাক। ম্যাক সাহেব রসায়ন, তড়িৎশক্তি,
বাষ্প চালিত ইঞ্জিন বিষয়ে বক্তৃতা দিতে থাকেন। তিনি শ্রীরামপুর কলেজে
একটি আধুনিক পরীক্ষাগারও স্থাপন করেন। ম্যাকের জনপ্রিয়তার এতদূর ছড়িয়ে
পড়ে যে, এশিয়াটিক সোসাইটি থেকেও আধুনিক চিন্তাবিদরা তাঁর বক্তৃতা শুনতে
শ্রীরামপুর আসতেন।
মাসিক দিগদর্শন পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে বিজ্ঞানের নানা দিকে ঘটতে থাকা
খবরাখবর দেওয়া হত। এই পত্রিকাতেই নিউটনের অভিকর্ষজ সুত্রের কথা বাংলা
ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্র, ধ্বনি-প্রতিধ্বনির উপর
অনেক সুখপাঠ্য প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার মাধ্যমে বাঙালি বেলুনে
আকাশ ভ্রমণ এবং বাস্প চালিত নৌকার কথা জানতে পারে সাধারণ মানুষ। স্কুল
বুক সোসাইটি শুধু মাত্র বাংলার বুকেই নয়, মাদ্রাজ ও বম্বেতেও স্থাপিত হয়।
এর অন্যতম প্রধান কারণ হল দেশীয় ভাষায় লেখা বইয়ের চাহিদা বাড়া। এর ফলে
ভারতের তিনটি অঞ্চলে যেখানে উপনিবেশ গড়ে উঠছিল, সেখানে বিজ্ঞান চেতনা
বিকশিত হতে থাকে।
রাজা রামমোহন রায় স্কুল বুক সোসাইটির কাছে বেকনের বিভিন্ন লেখা, যা
ইউরোপীয় বিজ্ঞানের বিকাশের আলোচনা সমৃদ্ধ ছিল, সেগুলি ভারতীয় ভাষায়
অনুবাদ করার গুরুত্ব উল্লেখ করেন।
রাম মোহন রায়ের পাণ্ডিত্যের প্রসিদ্ধি সারা ভারত তথা বিদেশেও প্রচার পায়।
দিল্লির বাদশাহ্ দ্বিতীয় আকবর রাম মোহনকে দিল্লিতে তাঁর দরবারে ডেকে
পাঠান। লন্ডনের রানির কাছে তিনি রাম মোহনকে দূত হিসাবে পাঠান পেনশন
বাড়ানোর আর্জি জানাতে। বাদশাহ্ রাম মোহনকে রাজা উপাধি দেন। ব্রিটেনের
রানির জন্য ইংরেজি আর্জি পত্র রাম মোহন লিখে দেন।
১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে রাম মোহন লন্ডন পৌঁছন রানির সাথে দেখা করবার
জন্য। সসম্মানে রাম মোহনের সাথে রানি দেখা করেন, কিন্তু আর্জি মঞ্জুর হয়
না। প্রথম ভারতীয় ব্রাহ্মণ লন্ডনের মাটিতে পা রাখেন। তদানীন্তন
ভারতবর্ষের সামাজিক পরিস্থিতিতে বিদেশের মাটিতে পা রাখা ছিল গর্হিত।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম রাম মোহনের আধুনিক দর্শনের কথা তাদের কাগজে ছাপতে
থাকে। লন্ডনের অভিজাত মহল রাম মোহন ‘ভারতের সাধু’ বলে পরিচিত হন। লন্ডন
সোসাইটিতে এবং নানা জায়গায় রাম মোহন বক্তৃতা দিতেন এবং পত্র পত্রিকায়
লিখতেন। তাঁর ইংরেজি ভাষার উপর অসামান্য দখল এই সময়ে জনপ্রিয়তা পায়।
হিন্দু দর্শনের নানা উন্নত দিক রাম মোহন মানুষের সামনে তুলে ধরে ভারত যে
একদা উন্নত দেশ ছিল, সেই কথা জানান জনসমক্ষে।
১৮২৯ সালে ভারতের মাটিতে সতীদাহ রদ করার যে বিল পাশ হয়েছিল, সেটি যাতে
বহাল থাকে, সেই ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে তিনি অনুরোধ জানান।
ইংল্যান্ডে বসবাস কালে সেখানকার আধুনিক দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের
সংস্পর্শে আসেন রাম মোহন। কিন্তু দেশে ফিরে আসা আর সম্ভব হয়নি তাঁর।
সেখানেই ম্যানেঞ্জাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৮৩৩ সালে মারা যান প্রকৃত
দেশপ্রেমিক রাজা রামমোহন রায়। তাঁর মৃত্যু ছিল সমাজ সংস্কারের এক যুগের
অবসান।